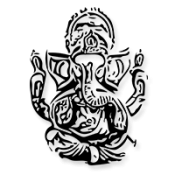বাঙালির প্রিয় উৎসব দুর্গাপুজো। দুর্গাপুজো ইতিহাস আজকের নয়। মাতৃ আরাধনার উল্লেখ পাওয়া যায় কালিকাপুরাণ, দেবীভাগবত পুরাণ সহ আরও অন্যান্য পুরাণে। যদিও বাংলায় যে রূপে মা পূজিত হন তাঁর প্রচলন অনেক পরে। এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন, শাস্ত্রে মাতৃ আরাধনার উল্লেখ রয়েছে বসন্তকালের শুক্লা তিথিতে। আবার অকালবোধনের সময় শক্তি পুজার যে কথা রামায়ণে আছে বলে আমরা জানি তাও কিন্তু বাল্মিকী রচিত মূল সংস্কৃত রামায়ণে নেই। সেই রামায়ণের বাংলা অনুবাদ, কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণে পাওয়া যায়।
বর্তমানে বাংলায় মা দুর্গা (Durga) পূজিত হন সপরিবারে। লোকবিশ্বাস, চার ছেলেমেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়িতে আসেন মা দুর্গা। তবে মাতৃ পুজোর এই ইতিহাস বেশি পুরোনো নয়। ১৪৮০ খ্রীস্টাব্দে রাজশাহী জেলার তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণের আমলে তাঁর বাড়িতে প্রথম এই পুজোর ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়। এমনকি দুর্গাপুজোর (Durga Puja) রীতিনীতিও নির্মাণ করেন রাজ পরিবারের কুলো পুরোহিত রমেশ শাস্ত্রী। আবার বাঙালি পণ্ডিত রঘুনন্দন রচিত ‘তিথিতত্ত্ব’ গ্রন্থে পুজোর বিধি পাওয়া যায়। মিথিলা বিজয়ী পণ্ডিত বাচস্পতি মহাশয়ের বইতেও সেই উল্লেখ পাওয়া যায়।
এরপর ক্রমে ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে কোচবিহারের রাজা বিশ্ব সিংহের আমলে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত দুর্গাবাড়িতে দুর্গাপুজোর ইতিহাস রয়েছে। ১৬০১ সালে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং ১৬১০ সালে বড়িশার জমিদার সাবর্ণ রায়চৌধুরী দুর্গাপুজোর প্রচলন করেন। তবে পুজোকে ঘিরে উৎসবে মেতে ওঠার চল শুরু হল ১৭৫৭ সালে শোভাবাজারের রাজবাড়িতে রাজা নবকৃষ্ণ দেবের মাতৃ পুজো শুরুর সঙ্গেই। সেই সময়ে পুজোকে ঘিরে রাতভর চলত নানা অনুষ্ঠান। কবিগান, বাঈজি নাচ, যাত্রাপালা, মল্লযুদ্ধ, মোরগ লড়াই থাকত আরও অনেক কিছুই। ক্রমে সেই দেখেই কলকাতার অনেক বাবুরাই নিজেদের বাড়িতে দুর্গাপুজো শুরু করেন। আর তারই সঙ্গে ইংরেজদের আমন্ত্রণ জানিয়ে চলত আমোদ-প্রমোদ।
ক্রমে এরই সঙ্গে মিশে গেল স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ। শুরু হল আজকের সর্বজনীন পুজোর। বাগবাজার সর্বজনীনের (Bagbazar Sarbojonin) পুজোকে ঘিরেই তার শুরু। সেই সময় পুজোগুলিকে কেন্দ্র করে বহু মানুষের আগমন হত। সেই ভিড়কে কাজে লাগিয়েই আয়োজন করা হত স্বদেশী মেলা। সিমলা ব্যয়াম সমিতির পুজোয় অষ্টমীর দিন থাকত লাঠি খেলা, তরোয়াল খেলা সহ আরও অনেক কিছুই।
সময় বদলেছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু পুজোকে ঘিরে মানুষের উন্মাদনা উৎসবের মানসিকতা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। দেশ, কাল, সীমানার গণ্ডি পেরিয়ে সেই উৎসব মুছে দিয়েছে জাতপাত, ধর্মের ভেদাভেদ।
আজ বঙ্গের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপুজো। পুজোর পাঁচ দিন থেকে বেড়ে সেই উৎসবের শুরু হয়ে যায় এখন মহালয়া থেকেই। সর্বজনীন পুজো আর সাবেকি প্রতিমার গন্ডি পেরিয়ে এখন থিম পুজোর রমরমা। এই পুজো যেন হয়ে ওঠে শিল্পের সঙ্গে ধর্মের মিলনের উৎসব। আলোর চাদরে ঢেকে যায় শহর কলকাতা। যে যেখানেই থাকুক না কেন পুজোর কটা দিন পরিবারের সঙ্গে কাটাতে চায় সকলেই।
দুর্গাপুজোর (Maa Durga) রীতিনীতির সঙ্গেই কিন্তু নিবির যোগ রয়েছে আরেকটি জিনিসের। তা হল পুজোর সাহিত্য। দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে পুজোর গান, পুজোর গল্প, পুজোর পত্রিকা, পুজোর নতুন বই- এই সবই কিন্তু দুর্গাপুজোর ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির অংশ। আবার মিতব্যয়ী মধ্যবিত্ত বাঙালির বেহেসাবী হয়ে ওঠার উদযাপন এই দুর্গাপুজো।
দুর্গাপুজো (Durga Puja 2024) বাঙালির রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমন ভাবেই মিশে গিয়েছে যে দেশের বাইরেও মাতৃ আরাধনায় মেতে ওঠে বাঙালি। বন্ধুদের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা, বন্ধুদের সঙ্গে জমিয়ে ভোগ খাওয়া, ঠাকুর দেখতে যাওয়া এই নিয়েই বাঙালির পুজো। আবার অষ্টমীর সকালে পাঞ্জাবি বা শাড়ি পরে প্রিয় মানুষের সঙ্গে অঞ্জলি না দিলে যে পুজোটাই অসম্পূর্ণ। অষ্টমী পেরোলেই সন্ধিপুজো। দেবীকে ১০৮ পদ্ম নিবেদন করার রীতি এই পুজোয়। এরপর নবমী পেরিয়ে দশমী। মাকে বিসর্জনের পালা। শোভাযাত্রা করে মাকে বিদায় জানানোর পালা। আর মনে মনে একটাই ডাক ‘তুমি আবার এসো মা!’
(লেখক সায়ম কৃষ্ণ দেবের প্রকাশিত লেখা)